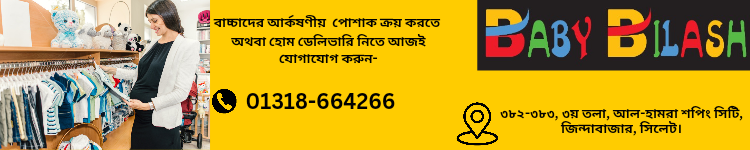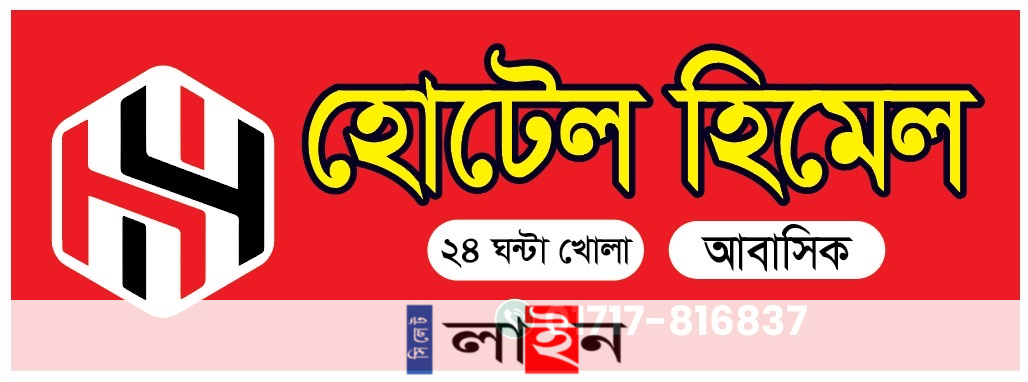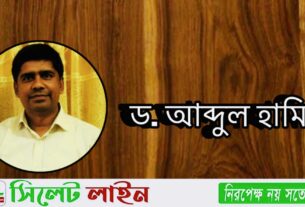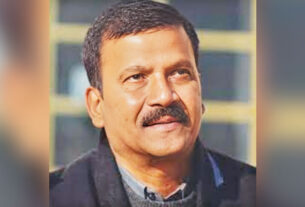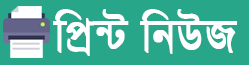
সভ্য পৃথিবীর যে কোনো ভূখণ্ডের মানবশিশু কোনো না কোনো ভাষিক পরিবেশে জন্ম লাভ করে। আদিম পৃথিবীর মানুষের ভাষা ছিল না বলে সেকালে শিশুরা জন্ম নিয়েই পিতামাতার ভাষার উত্তরাধিকারী হতো না। তাদের কোনো ভাষাশক্তি ছিল না। ইশারা-ইংগিতে, কোনো চিহ্নের সাহায্যে প্রয়োজন-অপ্রয়োজন ব্যক্ত করত। ভাষাভাষী কোনো ব্যক্তির নিজস্ব ভাষা ব্যবহারবিধি জন্মগত নয়। মানবশিশু ভাষাহীন অবস্থা থেকে ভাষার অধিকার অর্জন করে ক্রমবৃদ্ধির সমান্তরালে। প্রথমে একটি-দুটি অতি প্রয়োজনীয় শব্দ, অঙ্গ-উপাঙ্গ চারপাশের পরিবেশের অন্তর্গত বস্তু ও প্রাণীর নামের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তার বিচরণক্ষেত্র বাড়ার সঙ্গে প্রয়োজনের পরিধি বিস্তৃত হয়।
বৃদ্ধি পায় পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যক্ষণ ক্ষমতা– জাগতিক অভিজ্ঞতা অসীম বস্তুজগতের নিবিড় সান্নিধ্যে নিয়ে যায়। অতঃপর অভাববোধ থেকে জাগ্রত হয় চাহিদা প্রকাশের, দাবি জানাবার, প্রশ্ন করবার ও অনুসন্ধান করবার ক্ষমতা। ধীরে ধীরে মানবশিশু বুঝতে পারে তার অঙ্গ-উপাঙ্গের চেয়েও আরেকটি বলিষ্ঠ শক্তি রয়েছে, যা তার ইচ্ছাকে স্বাভাবিকভাবে ব্যক্ত করতে সাহায্য করে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু ঘটতে চাইলে সে ‘না’ বলে প্রচণ্ড শব্দে অস্বীকৃতি, প্রতিবাদ জানাতে পারে। প্রেমানুভূতি প্রকাশের যেমন ভাষা আছে, তেমনি আছে ভয়ংকরভাবে প্রতিবাদের ভাষা। মোলায়েম, নরম, স্নিগ্ধ, শ্রুতিসুখকর ভাষার বিপরীতে রয়েছে অস্বাভাবিক ঘৃণা, ক্রোধ, অগ্রাহ্য করবার উপযোগী ভাষা। মানুষ ভাষার শক্তিত্বে অন্যের সঙ্গে বিনিময়ের মধ্য দিয়ে তার আমিত্বের প্রতিষ্ঠা করে। ভাষা তাই শক্তি। এ-শক্তিরও রয়েছে ওজনের তারতম্য, গুরুচণ্ডাল ভেদ, অশালীন, শালীনরূপের প্রকাশ। ভাষা ব্যক্তিসত্তার এক বিশেষ ক্ষমতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতায় ব্যক্তিসত্তার বিস্ফোরন্মুখ জাগরণের অপ্রতিহত, দুর্নিবার, শক্তি অপরিমেয় ক্ষমতার অভিব্যক্তিরূপে চিত্রিত। সেই ক্ষমতার বিবিধ শক্তি জগতের নানাবিধ অবস্থা, রূপের, গতির মধ্যে উদ্ভাসিত হচ্ছে। ব্যক্তিসত্তার জাগরণের ভাষারূপটি নিম্নের চিত্রে গতি ও শক্তির অদ্বৈতরূপে অভিব্যক্ত– থরথর করি কাঁপিছে ভূধর,/শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,/ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল/গরজি উঠিছে দারুণ রোষে/… ভাঙ্ রে হৃদয় ভাঙ্ রে বাঁধন/ সাধ্ রে আজিকে প্রাণের সাধন,/লহরীর পরে লহরী তুলিয়া/ আঘাতের পর আঘাত কর্।’ এরই ভিন্নরূপ দেখি কাজী নজরুল ইসলামের ‘বিদ্রোহী’ কবিতায়। উদাত্তকণ্ঠের দৃপ্ত উচ্চারণ– ‘আমি চির-উন্নত শির!/আমি চিরদুর্দ্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,/মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,/…আমি ধূর্জ্জটী, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর!/ আমি বিদ্রোহী আমি বিদ্রোহী-সূত বিশ্ব-বিধাত্রীর!’ উদ্ধৃতি দুটিতে বাংলা ভাষার শব্দের ধ্বনিঝংকার, গুরুগম্ভীর ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা, চরণস্থিত শব্দপরম্পরা, আত্মিক অভিব্যক্তি প্রকাশের দৃঢ়তা, গতির প্রচণ্ডতা, ভাষার অন্তর্নিহিত আকর্ষণ ও ক্ষমতার উদ্ভাসন ঘটেছে।
নিয়মিত চর্চা ও সামাজিক বিনিময়ের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত ভাষার ক্ষমতার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও উৎকর্ষ সাধন সম্ভব। তা গোটাই অর্জিত বিষয়। কারণ ভাষা সামাজিকভাবে উৎপন্ন– স্বভাবজাত নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি সুনির্দিষ্ট সমাজপদ্ধতির অধীনে প্রচলিত রীতি-নীতি, প্রথা-সংস্কার, বিধিবিধান মেনে জীবন যাপন করতে হয়। ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা, স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজের সেই প্রচলিত নিয়মপদ্ধতিতে হয় বাধাগ্রস্ত। ফলে ব্যক্তির সঙ্গে সামাজিক নিয়ম ও রীতিপদ্ধতির সংঘাত সৃষ্ট হয়। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্ব, বিশেষ অবস্থায় ব্যক্তির বাহ্যিক বা সামাজিক অস্তিত্বের সঙ্গে তার মানসিক অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব– এই সকল দ্বন্দ্ব ব্যক্তিকে প্রথার বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলে। সেই বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটে প্রথমত ভাষার মাধ্যমে। কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস, হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গ রচনা, রম্যরচনার আঙ্গিকে। খ্রিষ্টপূর্ব কালে এথেন্সের যুদ্ধবাজ পুরুষদের বিরুদ্ধে নারীদের বিদ্রোহের আখ্যান ইউরিপিদেস রচিত নাটক লিসিসট্রাটা। সমকালের অপর নাট্যকার অ্যারিস্টোফেনিসের বার্ডস নাটক মানুষ ও দেবতাদের কর্মকাণ্ডের ওপর ক্ষুব্ধ বিদ্রোহী পাখিদের আকাশ-পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপনের ইতিবৃত্ত। এই রূপকের মধ্য দিয়ে সমকালের অবক্ষয়িত গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী এথেন্সের রাষ্ট্রনায়কদের তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা হয়েছে।
মানুষের চিন্তাশক্তির লিখিত রূপের মধ্যে ভাষাশক্তির প্রকাশ ঘটে। তা বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, দর্শন ও মূল্যবোধের তীব্র সমালোচনা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। কখনও হয় নতুন দার্শনিক তত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-সূত্রের বাহক। সমকালের মানুষ ভাষায় ধৃত বক্তব্যের মর্মার্থ যথার্থভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা কালে কালে যুগস্রষ্টা দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি সাহিত্যিক দণ্ডিত হয়েছেন। সর্বকালের সেরা দার্শনিক সক্রেটিস, স্টোয়িক দার্শনিক রোমান নাট্যকার সেনেকা, খ্রিষ্টধর্মের প্রবর্তক আধুনিক ইউরোপের অন্যতম প্রধান স্রষ্টা জিসাস ক্রাইস্ট দ্য নাজারাত, বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলেই প্রমুখ উল্লেখ্য।
ভাষার ক্ষমতা সহ্য করতে না পেরে পুরুষ শাসক কর্তৃক মহীয়সী খনার জিহ্বা কর্তন করে দেবার আখ্যান তো বাঙালি শিক্ষিতজনের বহুশ্রুত আখ্যান। সে আখ্যান গুপ্তযুগের ইতিহাসে প্রোক্ত। অব্যবহিত পরে ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকের মন্ত্রীর আদেশে আদি যুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কাহ্ন পাদের হাত কর্তনের ইতিবৃত্ত বর্ণবিদ্বেষ পরিপূর্ণ বাংলার সমাজ-জীবনের নিপীড়নের ভয়াবতার দৃষ্টান্ত। কাহ্ন পাদের অপরাধ সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে দেশি ভাষা অর্থাৎ জনসাধারণের মুখের ভাষা বাংলায় কাব্যচর্চা করা। মধ্যযুগের আলো-আঁধারির মধ্যে সুউচ্চ মানবতাবাদী আদর্শের বাণী উচ্চারণ করলেন অপর এক বাঙালি মরমি কবি চণ্ডীদাস– ‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।’ ভাষার কাজ তো শুধু বিদ্রোহের বাণী প্রচার করা নয়, তত্ত্বদর্শন প্রচার করাও নয়। প্রতিদিনের সংগ্রামশীল দুঃখময়, মানবেতর জীবনের তথ্যচিত্র উপস্থাপনও। এ-প্রসঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নয়নচারা গল্পের প্রসঙ্গ মনে পড়ে। ১৩৫০ বাংলা সনের মহামন্বন্তরে হতদরিদ্র নয়নচারা গ্রামের নিরন্ন মানুষের ভয়ানক অসহায় চিত্র লেখকের মর্মস্পর্শী দরদি বলিষ্ঠ ভাষায় এভাবে চিত্রিত হতে দেখি– ‘ময়রার দোকানে মাছি বোঁ-বোঁ করে। ময়রার চোখে কিন্তু নেই ননী-কোমলতা, সে-চোখময় পাশবিক হিংস্রতা। এত হিংস্রতা যে মনে হয় চারধারে ঘন অন্ধকারের মধ্যে দুটো ভয়ংকর চোখ ধক্ধক্ জ্বলছে। ওধারে একটা দোকানে যে ক-কাঁড়ি কলা ঝুলছে, সেদিক পানে চেয়ে তবু চোখ জুড়ায়। ওগুলো কলা নয়তো, যেন হলুদ-রঙা স্বপ্ন ঝুলছে। ঝুলছে দেখে ভয় করে– নিচে কাদায় ছিঁড়ে পড়বে কি হঠাৎ? তবু শঙ্কা ছাপিয়ে আমুর মন ঊর্ধ্বপানে মুখ করে কেঁদে ওঠে, কোথায় গো, কোথায় নয়নচারা গাঁ?’
উদ্ধৃতাংশের ভাষা প্রচণ্ড আবেগের স্রোতে ভেসে চলা কোনো রোমান্টিক প্রণয়ীর ভাষা নয়, উচ্চকণ্ঠ বিদ্রোহ-বিপ্লবের ভাষাও নয়, এর জাত আলাদা। নয়নচারা দুঃখের দোজখ- অভাবের আগুনে পুড়ছে। সমৃদ্ধ চাষিরা অভাবের যাতনায় নিরুপায় হয়ে গ্রাম ত্যাগ করে একমুঠো খাদ্যের জন্য শহরের বস্তিতে আশ্রয় নিয়েছে। এখানে সচ্ছল নাগরিক মানুষদের চোখে পাশবিক হিংস্রতা। আমুদের জীবনের শূন্যতা, তাদের দীর্ঘশ্বাসের মতো ক্লান্ত, কষ্টের মতো দহন করবার ক্ষমতা ভাষার গাঁথুনিতে নির্বাচিত শব্দ-পরম্পরায় বিধৃত। সেই মহাদুর্ভিক্ষের প্রকৃত অবস্থাটি অনুধাবনের জন্য কোনো সরকারি মহাফেজখানায় গিয়ে দলিল ঘেঁটে দেখার দরকার পড়ে না। গল্পের ভাষাই দুর্ভিক্ষপীড়িত, নিরন্ন, নিরাশ্রয় মানুষগুলোর অতীত জীবনের সঙ্গে বর্তমান অবস্থার একটি তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিত পাঠকের মানসজগতে মূর্ত করে। এই বিপর্যস্ত অবস্থাটি রচয়িতা সৃষ্টি করেন তাঁর নিজস্ব ভাষারীতির আশ্রয়ে, নির্বাচিত শব্দসহযোগে।
সাহিত্য ভাষা মাধ্যমে প্রকাশিত শিল্প। অর্থাৎ একমাত্র ভাষা মাধ্যমেই সাহিত্য সৃজিত হয়। সাহিত্যিকগণ বরাবর জাতির মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা করেন এবং সেটা রচয়িতারও মাতৃভাষা বটে। জাতির সদস্যদের সামাজিক কর্মময় জীবনের বিবিধ প্রাত্যহিক সমস্যার মর্মগত সত্যটি বিশেষরূপে উপস্থাপিত বস্তুর অভিব্যক্তি বলেই তা সাহিত্যের আদল পায়। সে অভিব্যক্তি ব্যক্তিক, সামাজিক, জাতীয় জীবনের এবং কখনও তা হয়ে থাকে বৈশ্বিক অর্থাৎ বিশ্বমানবতার (ইউনিভার্সাল বা হিউম্যানিস্টিক)। ভাষাগত ভিন্নতা, স্থানিক ও কালিক ভিন্নতা সত্ত্বেও সকল জাতির সাহিত্যের এটি এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সকল জাতির সাহিত্যই তার নিজ মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য। যে-জাতির ভাষা আছে কিন্তু লিপি বা বর্ণমালা নাই তাদের লিখিত সাহিত্য নাই। তাদের যে সাহিত্য আছে সেই সাহিত্যকে মৌখিক সাহিত্যের তালিকাভুক্ত করা হয়। ভাষার বর্ণমালা বা লিপি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা এ-কথা থেকেই বোঝা গেল। সাহিত্য সৃষ্টির জন্য মাতৃভাষার গভীর জ্ঞান থাকা জরুরি। তাছাড়া দীর্ঘ দিনের চর্চায় নিজের একটা ভাষারীতি নির্মাণ করা চাই। মনে রাখতে হবে– ভাষা সাহিত্য সৃষ্টির মৌল উপকরণ। ভাব, বিষয়, চরিত্র সৃষ্টিতে দক্ষ কোনো সাহিত্যিক যদি উৎকৃষ্ট ভাষাজাত শৈলী নির্মাণে সফল হতে না পারেন তবে সে স্রষ্টা সর্বাংশে ব্যর্থ।
তাই প্রত্যেক যুগের সাহিত্যই সেই বিশেষ যুগটির প্রকৃত ও বিশ্বস্ত উপস্থাপনা ভিন্ন আর কিছু নয়। তার অর্থ– সেই যুগের যাবতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, নৈতিক সমস্যা, রাজনৈতিক ও পরদৈশিক বা পররাষ্ট্রবিষয়ক সমস্যা, যুগগত চাহিদা ও রুচির আলোকে শিল্প প্রতিভার কৌশল ও উপস্থাপনার জাদুতে সাহিত্যে উপস্থাপিত হয়। যেমন– দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীল দর্পণ’ নাটক, মীর মশাররফ হোসেনের ‘জমিদার দপর্ণ’ নাটক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাস, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পথের দাবী’ উপন্যাস, ম্যাক্সিম গোর্কির ‘মা’ আলব্যে’র কামুর উপন্যাস ‘আউটসাইডার’ ইত্যাদি। একই সমাজের উপস্থাপনা সত্ত্বেও সাহিত্যের প্রতিটি সৃজন নতুন এবং একে অপর থেকে আলাদা। আলাদা হবার কারণেই রসগ্রহণে পাঠকের উৎসাহের অন্ত নাই। শিল্পী ব্যক্তি আলাদা বলে শিল্পকর্ম দুটি আলাদা হতে পারে। কেবল দৃষ্টিভঙ্গি ও বিষয়ের স্বাতন্ত্র্যের জন্য পরস্পর আলাদা হতে পারে একই ব্যক্তির দুটি ভিন্ন সৃষ্টিও। ভাষা অভিন্ন হলেও রীতি বা স্টাইল উভয় ক্ষেত্রেই ভিন্ন হতে পারে।
শিষ্ট শিক্ষিতজনের ভাষা প্রমিত ভাষা। তারা শ্লীলতা বজায় রেখে নানা কৌশলে নিজস্ব বক্তব্য প্রকাশ করেন। সে ভাষা প্রায়শই আভিধানিক ভাষা– তাকে এক ধরনের মুখোশ বলা যায়। নিম্নবিত্ত মানুষ দেশের জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। তারা আবেগ, ভাবাবেগ বর্জিত নয়– মানুষ হিসেবে তাদেরও পছন্দ-অপছন্দ রয়েছে। স্বাধীনসত্তার অধিকারী একজন ব্যক্তি মানুষ কোনো সমাজনীতি, রাষ্ট্র জারিকৃত কোনো আইন বা প্রজ্ঞাপনের বিরোধিতা করতেই পারেন। সে ক্ষেত্রে ভাষাটি শিক্ষিত নাগরিকের মতো নিশ্চয়ই পরিশীলিত, প্রমিত না হওয়াই স্বাভাবিক। তাই বলে এই নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত নাগরিকের ভাষা শক্তিহীন এরূপ ভাবা অনুচিত। সমষ্টির বা ক্ষমতাকেন্দ্রের চাপিয়ে দেওয়া কোনো নির্দেশ অবগত হয়ে একজন নিরক্ষর মানুষ একটি অশালীন উক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর ক্রোধের প্রকাশ ঘটাতেই পারে। এই অশালীন উক্তিটি তাঁর প্রতিবাদ হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। কারণ তাঁর সামাজিক স্তর জীবনযাপন প্রণালি তাঁর ভাষাচেতনার নিয়ন্তা। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘ফেরারী’ গল্পের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা যেতে পারে– অনেকক্ষণ চুপচাপ হেঁটে হাইকোর্টের সামনে এসে ডামলালু চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, ‘চুতমারানি!’। বিগলিত গলায় হানিফ উত্তর দেয়, ‘প্ পুলিসে আইয়া পড়লো, ন্ নইলে ঐ রিক্শার মইদ্যে ম্ মালপানি বহুত ম্ মিলতো, না ওস্তাদ?’ ডামলালু অবাক হলো ‘পুলিস পাইলি কৈ?’ ‘জজিপগাড়ির মইদ্যে প্ পুলিসে আছিলো না? ‘আমার ল্যাওড়া আছিল! জিপগাড়িটা দেখছিলি ভালো কইরা? দেখছিলি?’
চরিত্রের ভাষা হিসেবে গল্পকারের এই ভাষা অনেক বেশি শক্তিশালী ভাষা, যা শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে। প্রমিত ভাষার চেয়ে লোকভাষা বা উপভাষার সামর্থ্য অধিক। কেননা শ্রম ও ঘামে উৎপন্ন প্রতীক সে ভাষার শব্দভান্ডারে গড়া।
লেখক: শিক্ষাবিদ প্রাবন্ধিক
শেয়ার করুন